পুরনো কেল্লার পুরনো গল্প - অথ ফোর্ট উইলিয়াম কথা [তৃতীয় পর্ব]
"অনেক ধুলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।"
- প্রেমেন্দ্র মিত্র
পুরনো কেল্লা ছিল কাগুজে কেল্লা, তার না ছিল কোন পরিখা না ছিল সামান্য প্যালিসেডের ঘের। চারদিকের চারটি বুরুজে এবং প্রাকারে কামান বসানো থাকতো বটে, এইটুকুই! কিন্তু সাদামাটা হলেও সে আমলের ছবিগুলি দেখে এটুকু বিশ্বাস করাই যায় যে গঙ্গার তীরে বেশ মনোরম দৃশ্য তৈরি করতো পুরনো কেল্লাটি।
কেল্লার প্রাকারগুলি একটি অসমবাহু চতুর্ভুজ তৈরি করেছিল। এর পূর্ব প্রাকার ছিল পশ্চিম প্রাকারের চেয়ে দীর্ঘ আবার দক্ষিণ প্রাকারটিও ছিল উত্তর প্রাকারের চেয়ে লম্বা! ‘দ্য স্টোরি অফ দ্য ভাইসরয়’স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট হাউসেস’ গ্রন্থে লর্ড কার্জন প্রথম কুঠির বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন, “The Factory building itself was two storeys in height, all the main apartments being upon the upper floor. On entering by the main doorway on the riverside, you turned to the left and ascended by the great staircase to the central hall, from which the principal buildings, lit by very long windows, branched out on either side. On the Eastern face a raised verandah or arcade ran round the three sides of the interior quadrangle. The Governor’s apartments were situated in the South-east wing, but were of no great size, and in the later years, before 1756, were rarely occupied by him, being in all probability used as offices alone. ”
উদ্ধৃতির শেষের বাক্য থেকে এই কেল্লার বিরাট একটা দুর্বলতা বোঝা যাবে যা রীতিমত আশ্চর্যের। তা হল ফোর্টের ভিতরে দুর্গাধীপ বসবাস করতেন না। বস্তুত ইতিহাসও সেকথাই বলে; আয়ার বা বিয়র্ড সাহেবের মতো প্রথম দিকের গভর্নররা কেল্লা তৈরির সময় ভিতরে ঘাঁটি গেড়ে থেকে কাজ পরিচালনা করতেন। কেল্লার চারপাশে তখন একই সঙ্গে হোয়াইট টাউন গড়ে উঠছে, তৈরি হচ্ছে রম্য অট্টালিকার সারি। পরবর্তি গভর্নররা কেল্লার বাইরে থাকাই পছন্দ করতেন কারণ কুঠি বাড়িটি যথেষ্ট কেতা দুরস্ত নয়। ইতিমধ্যে কেল্লা সংলগ্ন চার্চ তৈরি হয়েছে, যার কথায় পরে আসছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য মায় গভর্নর অবধি রয়ে গেলেন কেল্লার বাইরে অরক্ষিত অবস্থায়! এই সব কারণেই তৈরি হতে না হতেই স্তুতি ও নিন্দা দুই জুটতে লাগলো পুরনো কেল্লার।
ক্যাপ্টেন অ্যালেকজান্ডার হ্যামিল্টন যাকে সিন্দাবাদের অষ্টাদশ শতকীয় সংস্করণ বলা হয় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন কলকাতার পটভূমিতে ১৭০৯ সালে। পরবর্তিকালে তার ‘এ নিউ অ্যাকাউন্ট অফ ইস্ট ইন্ডিজ’ নামক ভ্রমণকাহিনীতে তিনি লিখেছিলেন, “The Governor’s House in the Fort is the best and most regular piece of architecture that I ever saw in India.”
সারা ভারতে এমন স্থাপত্য আর দেখেননি হ্যামিলটন এহেন বক্তব্য আমাদের কাছে হাস্যকর লাগলেও স্বাভাবিক ভাবেই উইলসন, কটন ইত্যাদি সাহেবকুল এই উক্তিটি দিয়ে তাদের পুরনো কেল্লার প্রশস্তি গেয়েছেন।
অন্যদিকে লিডেনহল স্ট্রিটের কর্তারা কেল্লা পরিদর্শন করে বেশ কড়া সমালোচনা করলেন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মন্তব্য করে, “A very pompous show to the waterside by high turrets of lofty buildings, but having no real strength or power of defence.”
গভর্নর ভিতরে থাকুক বা বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ঘাঁটি হিসেবে ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠতে থাকলো। মালবাহী জাহাজের আনাগোনা কেল্লার ঘাটে বাড়তে লাগলো। কর্মচারী সংখ্যাও বাড়াতে হল উত্তরোত্তর। আচ্ছা, কারা সেখানে কাজ করতো একবার খোঁজ নেওয়া যাক!
কোম্পানির সাধারণ চাকুরেদের শ্রেণী বিভাগ ছিল মূলত চার ধরনের। রাইটার, ফ্যাক্টর, জুনিয়ার মার্চেন্ট এবং সিনিয়র মার্চেন্ট। সবাইকে রাইটার অর্থাৎ ‘ডেসপ্যাচ রাইটার’ হয়েই প্রথম ঢুকতে হত। ইংল্যান্ড থেকে রাইটারের চাকরির পেতে ইচ্ছুক যুবকেরা কেল্লার ঘাটে নামতো এহেন সুপারিশ পত্র নিয়ে –
“Having been duly educated in Writing, Arithmetic and Merchants accounts he is desirous in serving Your Honours as a Writer in India & prays therefore to be admitted accordingly, being ready to give the security required.”
রাইটার হয়ে ঢুকে দ্রুত উন্নতি করে এবং ন্যায্য অন্যায্য বহুবিধ পদ্ধতিতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হওয়ার উদাহরণ আছে বিস্তর। রিচার্ড বারওয়েল, হেনরি ভ্যন্সিট্যার্ট, উইলিয়াম থ্যাকারের মতো কোম্পানির অসংখ্য কর্তা ব্যক্তি প্রথম রাইটার হিসেবেই কাজে ঢোকেন। এই কারণেই কাতারে কাতারে ইংরেজ তরুণ জীবন বাজি রেখে সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এই প্রতিকূল পরিবেশে হাজির হতে দ্বিধা করতো না।
এবার আসি এই শহরের প্রথম যিশুর উপাসনালয় সেন্ট অ্যান চার্চ প্রসঙ্গে। আগেই জানিয়েছি ফোর্ট উইলিয়ামের বাইরে ছিল গির্জাটি, পূর্ব দিকে ফোর্টের যে প্রধান প্রবেশ পথ তার কাছাকাছি। বর্তমানে রাইটার্স বিল্ডিঙের পশ্চিমার্ধ এই চার্চের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।
উইলসন লিখেছেন, “The church of St. Anne, which stood immediately outside the fort before the east curtain wall, was built in the days of rotation government, and consecrated on the Sunday after Ascension Day, June 5,1709.”
আশ্চর্যের বিষয় হল বলা হয়ে থাকে শহর কলকাতার প্রথম অ্যাংলিকান চার্চ হল সেন্ট জন'স চার্চ। অর্থাৎ কোম্পানি স্থাপিত প্রথম গির্জা সেন্ট অ্যান চার্চ তার মানে আর যাই হোক অ্যাংলিকান ছিল না। এটা কি করে সম্ভব হল!? যে সব লেখা থেকে সেই সময়ে কোম্পানি কর্মকর্তাদের মনস্তত্বে উঁকি দেয়া যায় সেখানে এই নিয়ে কোন মন্তব্য নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে রাজশক্তির ধর্ম সাধারণের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। এবং কোম্পানির ধর্মীয় মতামতের নিজস্ব পরিধির মধ্যে সম্ভবত ব্রিটিশ রাজপরিবার মাথা গলাতো না। তবে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য তথ্য হল বলা হচ্ছে গির্জাটি তৈরি হয়েছিল “by the pious charity of merchants residing there, and the Christian benevolence of seafaring men whose affairs call them to trade there.” অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং নাবিকদের অর্থে তৈরি হয় প্রথম চার্চ। শুধু মাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পয়সায় নয়। সুতরাং তা অ্যাংলিকান হওয়ার প্রশ্নই আসেনি তখন।
এবার আসি এই প্রথম গির্জাটি যে সন্তের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে। তাঁর চয়নের মধ্যে দিয়ে কোম্পানি ওয়ালাদের মনেরছবি কিছুটা পাওয়া যাবে। সেন্ট অ্যান হলেন মেরির মা অর্থাৎ যিশুর মাতামহী। তিনি ঝড়ের দেবী ও নাবিকের রক্ষাকর্ত্রী। কার্পেন্টার, মাইনারদের মতো যারা কায়িকশ্রমের কাজ করে তাদের প্যাট্রন সেন্ট তিনি! তাঁর পোর্ট ফোলিওতে আরও পড়ে অবিবাহিতা নারী, সন্তান সম্ভবা মায়েদের দায়িত্ব। এবার বোঝা গেল এই বিজন বিভূঁই দেশে প্রথম উপাসনালয়টি কেন সেন্ট অ্যানকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। দলে দলে নাবিক তখন ভিড় করেছে এখানে। ভাগ্যান্বেষণে সাগর পাড়ি দিয়ে এদেশে ভিড়ছে অসংখ্য যুবক। প্রসঙ্গত জানাই মাদ্রাজের চার্চটিও সেন্ট অ্যানের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল যেখানে জোব চার্নকের কন্যাদের ব্যপ্টাইজড করা হয়।
সেই সময় চিত্রটা এমন ছিল যে যদি আগাম খবর পাওয়া যেত যে জাহাজে যুবতীরা আসছে তো সাজো সাজো রব পড়ে যেত। চাঁদপাল ঘাটে গোঁফে আতর লাগিয়ে কে আগে প্রাণ করিবেক দান বলে হত্যে দিয়ে থাকত রাইটাররা। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কলকাতায় বসবাসরত শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার পুরুষ নারীর অনুপাত ছিল সাড়ে চার হাজার পুরুষ পিছু মাত্র আড়াইশো নারী। সহজেই অনুমেয় এথেকে যে প্রথম দশকগুলোতে আরও কম ছিল সংখ্যা। এমতাবস্থায় সেন্ট অ্যানের অনুগ্রহ একান্ত কাম্য। তারা চেয়েছিল আগে তো ঝড় বাদলে, জাহাজ ডুবিতে না মরে করে কম্মে বাঁচি, একটি সৎপাত্রী জোটাই, বংশ বৃদ্ধি করি তবে অন্য দিকে তাকানো যাবে! ধন্য ‘অর্থ’ কুহকিনী!
©প্রজ্ঞা পারমিতা
তথ্য ঋণঃ
টাউন কলকাতার কড়চা - বিনয় ঘোষ
Old Fort william in Bengal by C R Wilson
ছবিঃ
জর্জ ল্যাম্বার্ট অঙ্কিত সেন্ট অ্যান গির্জা
পুরনো কেল্লার প্ল্যান
[ক্রমশ]


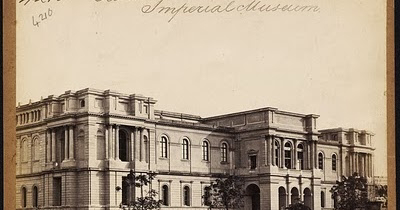

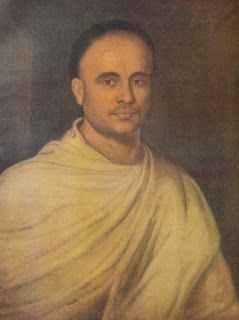
তথ্য সমৃদ্ধ খুব ভালো লেখা
ReplyDelete